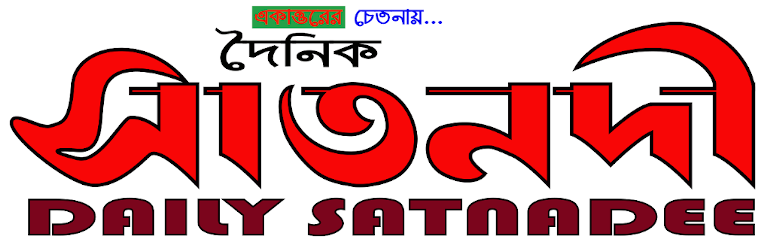
বাস্তবতার সাথে টিকে থাকতে পারছে না আশাশুনির হাতপাখার কারিগররা
সচ্চিদানন্দদেসদয়,আশাশুনি থেকে: বিদ্যুতের যুগেও বৈদ্যুতিক পাখার পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের মানুষের কাছে একটু কদর কমেনি তাল পাখার। বরং বিদ্যুতের লোড সময় মানুষের কাছেই বৃদ্ধি পেয়েছে এর চাহিদা। আর এ কারণেই সাতক্ষীরাে জেলার আশাশুনি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অনেক পরিবার পাখা তৈরি ও বাজারজাত করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।কিন্তু করোনার কবলে পড়ে অসহায় হয়ে পড়েছে এ পেশার সাথেযুক্ত কারিগর রা। অপরদিকে বিলুপ্তির পথে তালপাতার হাতপাখা । বর্তমানে প্লাাষ্টিকের হাত পাখা প্রচলন হলেও তালের হাত পাখা বা খেজুর পাতা, কাপড়ের তৈরি পাখার মর্যাদা নিতে পারেনি।এ বছর চরম মন্দার কবলে আশাশুনির হাতপাখা গড়ার কারিগররা। করোনার ছোবলে সরকারী লকডাউনে বাজার মন্দা, ফলে চাহিদা নেই হাত পাখার। বাজারে হাতপাখার চাহিদা না থাকায় মাথায় হাত এই পেশায় যুক্ত পরিবার গুলির। বিদ্যুৎ চালিত পাখার দাপটে এমনিতেই গৃহস্থের ঘর থেকে হারিয়ে গেছে তাল পাতার হাতপাখা।হাতপাখার বিবর্তনের ইতিহাস আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে। এমনকি গ্রিক রোমানদের যুগেও এই হাতপাখার প্রচলন ছিল। প্রথম দিকটায় পাখাগুলো ছিল একটা সম্পূর্ণ অংশ। ভাঁজ বা ফোল্ডিং পাখা এসেছে আরো অনেক পরে। ইউরোপীয় বণিকরা প্রথম এই ধরনের পাখা নিয়ে আসে চীন ও জাপান থেকে।তখন এসব পাখা বেশ দুর্মূল্যই ছিল। এগুলোতে ব্যবহার করা হতো মণিমুক্তো ও হাতির দাঁত। সোনা-রুপার পাত বসানো হাত পাখাগুলোয় নিপুণ হাতে শিল্পীরা আঁকতেন সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চেতনা কিংবা ধর্মীয় নানা কাহিনী, ফুল লতাপাতাসহ সমসাময়িক নানান বিষয়াবলী। আঠারো শতকের গোড়া থেকে ইউরোপে হাতপাখা তৈরি শুরু হয়। তবুও চীন থেকে আসা পাখার আবেদন তখনও ছিল তুঙ্গে। এই ইংরেজ আমলে এমন কি ইংরেজ আমলের পরেও জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এ ধরনের পাখা টেনে বাতাস করার ব্যবস্থা ছিল। তখন এ কাজের জন্য সরকারি কর্মচারীও নিযুক্ত ছিল। এখন এই ধরনের পাখা অনেক কম দেখা যায়। তবে গ্রাম বাংলায় হাত পাখার কদর এখনো কমে নি। কৃষক মাঠে কাজ করছে, আর স্ত্রী স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে আসছে এবং সাথে একটি হাত পাখা। কৃষক খাচ্ছে আর গৃহবধু হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে। এই ছবি যেন মনে দাগ কেটে যায়। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রাখার মতো যে পাখা সেটি রঙিন সুতোর ‘নকশি পাখা’। অনেকটা নকশিকাঁথার মতো। তবে পাখা যেহেতু ছোট, সেহেতু সেখানে কারুকাজের সুযোগও কম। তবে সুতো দিয়েই পাখার গায়ে পাখি, ফুল, লতা-পাতা কিংবা ভালোবাসার মানুষের নাম অথবা ভালোবাসার চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা হয়।তালপাতার পাখা তৈরির কারিগর আশাশুনির শে^তপুর গ্রামের মোঃ আব্দুল গফুর সরদার জানান, তালপাখা তৈরিতে দরকার হয় তালপাতা, বাঁশের শলাকা, কঞ্চি, সুতা-সুই ও রং। প্রথমে শুকনা তালপাতা কয়েক ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে জাত দিতে হয়। জাত বা জাগ দেয়া শেষে তালপাতা পানি থেকে তুলে বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে কলম লাগিয়ে রোদে শুকানো হয়। এরপর ধারালো ছুরি দিয়ে গোল করে ছেটে আগে থেকে রং করে রাখা বাঁশের শলাকা দিয়ে সুই-সুতাই বাঁধা হয়। পাখাকে আকর্ষণীয় করতে বিভিন্ন রংয়ের সুতা দিয়ে নকশা করা হয়ে থাকে। তবে নিজস্ব পুঁজি না থাকায় অধিকাংশ পাখার কারিগর এ শিল্পে শ্রম বিক্রি করে থাকেন। জাত দেয়া থেকে শুরু করে কলম ও গোল দেয়া পুরুষ শ্রমিকদের কাজ। একজন পুরুষ শ্রমিক ১শ’ পাখার কাজ করে মজুরী পান ২০০শ’ টাকা থেকে ৩০০টাকা। একজন পুরুষ শ্রমিক দিনে সর্বোচ্চ ১শ’ টি পাখার কাজ করতে পারেন। পাখা বাঁধাইয়ের কাজ করেন মহিলা শ্রমিকরা। ১শ’ পাখা কাজ করে মহিলা শ্রমিকরা মজুরি পান ১০০ থেকে ১২০ টাকা। একজন মহিলা শ্রমিক দিনে ৬০ থেকে ৭০ খানা পাখা বাঁধতে পারেন।শে^তপুর গ্রামের আব্দুল গফুর সরদার জানান, তালপাখার জন্য ছোট গাছের পাতার চাহিদা বেশি। আগে এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত তালপাতা পাওয়া গেলেও এখন আগের মত পাতা মেলেনা। দুর-দুরান্ত থেকে পাতা কিনে আনতে হয়।পাখার বাতাসে প্রাণ যেমন জুড়ায়, তেমনি বাহারি সব পাখা দেখে চোখও জুড়ায়।কত রকমের পাখা থাকতো সেই সময় বাড়িতে, কাপড়ের পাখা, বাঁশের চাটাইয়ের রঙিন পাখা, তালপাতার পাখা, ভাজ পাখা, চায়না পাখা, ঘোরানো পাখা। প্রচন্ড গরমে তাল পাতার পাখা জলে ভিজিয়ে তালের হাত পাখার বাতাস প্রাণ জুড়ুুয়ে দেয়, বিদ্যুৎ থাকলেও গ্রামে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো আছেই। তাই হাত পাখার প্রচলন কমে গেলেও শেষ হতে পারেনি।
Copyright © 2026 দৈনিক সাতনদী. All rights reserved.